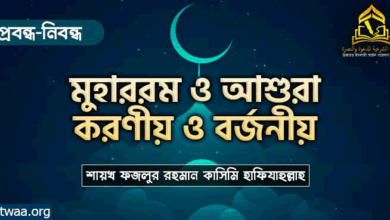ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কেন ওয়াজিব?[তৃতীয় পর্ব-২য় ভাগ]
ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কেন ওয়াজিব?

[তৃতীয় পর্ব-২য় ভাগ]
শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ
ইতিহাসের উল্লিখিত অংশের সাথে আমরা যুক্ত
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের যে অংশটি আমরা উল্লেখ করে আসছি, তা সে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটি অংশ এবং হিন্দুস্তানের লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল থেকে শুধু ছোট্ট একটি ভূখণ্ডের ইতিকথা যার সঙ্গে আমরা যুক্ত এবং যার সঙ্গে আমাদের দীনী, ইলমী, ইসলাহী ও দাওয়াতী যোগসূত্র রয়েছে। এছাড়াও আরও শত শত কারগুজারি রয়েছে যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো। কিন্তু এখানে আমরা শুধু উদাহরণস্বরূপ কিছু তুলে ধরতে চাই, যা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।
ইতিহাসের এ অংশ এবং এ ধরনের অন্যান্য উদাহরণ থেকে নিম্নোক্ত কথাগুলো খুব স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উঠে আসে-
০১. মোগল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন এবং ইংরেজদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা দখলের পরও দারুল ইসলাম পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য হিন্দুস্তানের আনাচে-কানাচে বিভিন্নভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলমান থাকে।
০২. শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ-এর মৃত্যু, অর্থাৎ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুস্তান দারুল হারবই ছিলো এবং তা পুনরায় দারুল ইসলামে রূপান্তরিত তথা পরিবর্তিত হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।
০৩. মুনাফিকরা তাদের নিফাক ও গাদ্দারিতে তৎপর রয়েছে।
০৪. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সারির সন্তান এবং প্রথম সারির মুখপাত্র হিসাবে, এমনিভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও শামেলীর ময়দানের মুজাহিদগণের একজন উপযুক্ত ওয়ারিস হিসাবে শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ পৃথিবীর মানুষদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব কী, তাদের চিন্তা-ফিকির কোন পথে কোনভাবে চলবে এবং তাদের কর্মপদ্ধতি কী হবে?
মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের দুর্গন্ধ
আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পর থেকে নববী পদ্ধতিতে সশস্ত্র জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার অনুসৃত পদ্ধতিতে কাজ করার চিন্তা-ফিকিরের মাঝে কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এ পর্যায়ে পাঠকবর্গ স্মরণ রাখা চাই যে, এটা সে সময়, যখন গণতন্ত্রের দুর্গন্ধ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং হিন্দুস্তানও সে দুর্গন্ধে প্রভাবিত ছিলো। কাফেরদের সহস্র অপকর্মের মাঝে গণতন্ত্রের অসারতা বিশেষভাবে অনুভব হত না। কিন্তু মুসলমানদের স্বচ্ছ সুন্দর দীন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শরীয়তের মাঝে এ গণতন্ত্র প্রাণবিনাশী বিষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
কামাল আতাতুর্কের মতো মুলহিদ-মুরতাদ ও ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামী খিলাফতকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলার জন্য গণতন্ত্রের কৌশল ব্যবহার করে। কাফের বন্ধুদের মাধ্যমে সে আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। যেসব জাহেলী প্রথা-প্রচলনকে ইসলাম পায়ে পিষে ফেলেছিলো, এই খবিস সেসব জাহেলী প্রথা-প্রচলনকে গণতন্ত্রের ছত্র ছায়ায় আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে এবং ইসলামের সকল নিশানা ও চিহ্নকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য সব ধরনের পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে।
যাই হোক, এ উপাখ্যান অনেক দীর্ঘ। আমরা এর বিবরণে জড়াতে চাই না। শুধু পৃথিবীর তৎকালীন চলমান অবস্থার একটি চিত্র পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরা উদ্দেশ্যেই প্রাসঙ্গিকভাবে এসব ব্যক্ত করলাম। যাতে সংশ্লিষ্ট কথাগুলো বোঝা সহজ হয়।
একটি দুঃখজনক বাস্তবতা
এ সময়ের আরেকটি দুঃখজনক বাস্তবতা দৃশ্যমান, যা স্বীকার না করে কোনও উপায় নেই। তা হচ্ছে, শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর শেষ যমানা পর্যন্ত রাজনীতি, নেতৃত্ব, ইসলামী শরীয়ার প্রয়োগ, খিলাফত ও ইসলামী ইমারতের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ের ফরিযা ও দায়িত্ব একটি শরয়ী যিম্মাদারী ও দায়িত্ব হিসাবে উলামায়ে কেরাম ও দাঈ ও শরীয়তের রাহবারগণ শতভাগ নিজেদের হাতে রেখেছেন এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করেছেন। তখন প্রতিটি বিষয়কে তাঁরা শুধু এবং শুধুই কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে দেখতেন।
শরীয়তের মানদণ্ডে বিচার করতেন এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে যা সঠিক মনে করতেন তা বাস্তবায়ন করতেন, এর বিপরীত সব কিছুকে ত্যাগ করতেন। তখন সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র শরীয়তই ছিলো। আর তারই আলোকে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা হতো না এবং শরীয়তের বাতলানো সীমানাকেই নিজেদের বিচরণের সীমানা হিসাবে মেনে নিতেন।
কিন্তু এর পরবর্তীতে অবস্থা কিছুটা এমন হয় যে, বলা যায়, উলামায়ে কেরাম এবং সত্য দীনের রাহবারগণ সত্য বলা, জান কুরবান করা, জিহাদের জযবা ও উদ্দীপনা, শরীয়তের আনুগত্য, মোটকথা সর্বক্ষেত্রে শরয়ী যিম্মাদারীর প্রাপ্য হক তাঁরা আদায় করতে থাকেন, কিন্তু ধীরে ধীরে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁদের হাত থেকে বের হয়ে যেতে থাকে।
মাশায়েখে ইসলাম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ
তৎকালীন নেতৃত্বশীলরা নিজেদেরকে একজন মুসলিম রাহবার মনে করে, মুসলিম রাহবার হিসাবে পরিচয় দেয়ার পরিবর্তে একজন সফল নেতা হিসাবে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করতো। এসব নেতার মধ্য থেকে যারা মুসলিম ছিলো, তারা দীন ও শরীয়তকে সম্মান করত, নিজের ধর্মকে ভালোবাসতো এবং তার উপর আমলও করত, ইসলামের পক্ষে তাদের অসংখ্য অবদানও রয়েছে। কিন্তু তারা সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তকে হাকেম তথা সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোকে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে সমাধান দেওয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলো না। তাদের কথাবার্তা ও চিন্তা-চেতনায় কুরআন-হাদীস ও দীন-শরীয়তের কোনও প্রভাব দেখা যেত না।
তারা উলামায়ে কেরাম ও মুসলমানদের দীনী রাহবারগণের জযবা ও উদ্দীপনাকে নিজেদের পার্থিব চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্যগামী করায় প্রয়াসী ছিলো। দুনিয়াবি নেতা হিসাবে যেসব চিন্তা-ভাবধারা ও পদক্ষেপের মধ্যে তারা সম্পৃক্ত ছিলো এবং যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তারা লিপ্ত ছিলো, সেসবের জন্য দীন ও শরীয়তের কিছু বহাল থাকুক অথবা না থাকুক, তা নিয়ে তাদের কোনও ফিকির ছিলো না। এরূপ ছিলো তাদের কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপের বাস্তবতা।
যাই হোক এ পর্যায়ে আমি দুটি কথা পেশ করছিলাম-
* একটি হচ্ছে, শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়টি এমন কিছু মানুষের হাতে পর্যবসিত হয়, যারা রাজনৈতিক নেতা হলেও মূলত তারা মুসলমানদের রাহবার ছিলো না। তারা ইংরেজদের থেকে হিন্দুস্তানকে স্বাধীন করতে চাইতো, কিন্তু কাফেরদের থেকে মুসলমানদেরকে স্বাধীন করতে চাইতো না। তারা কাফেরদের আধিপত্য খতম করতে চাইতো, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর আইন তথা ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাইতো না। এটা ঠিক যে,তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চাইতো না, কিন্তু তারা ইসলামী খিলাফতও চাইতো না। তারা ইংরেজদের শাসন থেকে হিন্দুস্তানকে মুক্ত করতে প্রয়াসী, কিন্তু সেই হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম বানাতে চাইতো না। এগুলো ছিলো তাদের পদক্ষেপ-কর্মকাণ্ডের প্রয়াস পরিসর। এটি হচ্ছে প্রথম কথা।
* আমি দ্বিতীয় যে কথাটি বলছিলাম তা হচ্ছে, এ পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরাম ও উম্মতের রাহবারগণ কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েন। কেউতো ভালো কিছুর আশায় পেরেশান হয়ে পড়েন। কোনো না কোনোভাবে মুসলমানদের জন্য কিছু করতে চাইতেন। কেউ কেউ নেতাদের চাপাবাজিতে ধোঁকা খেয়ে প্রতারিত হন। কেউ নিজেদের দাবি আদায়ের বিষয়ে নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। আর কেউ সেসব নেতার হাতে নেতৃত্ব সঁপে দেওয়া ব্যতীত আর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আর এগুলো ছিলো উলামায়ে কেরাম ও উম্মতের রাহবারদের অসহায় দশার ফিরিস্তি।
মূলত বাস্তবতা এই দাঁড়ায় যে, খিলাফত-রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিষয়গুলোতে উলামায়ে কেরাম এক প্রকার বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। আর বিরক্তির ছাপ তাঁদের মাঝে প্রকাশ পাচ্ছিলো। সেই সঙ্গে রাজনীতি ও ইমারাতের বিষয়াদিতে তাঁদের আগ্রহ-উদ্দীপনা অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। বলা যায়, শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পর থেকে অধঃপতনের এ পরিস্থিতি তিনটি পর্বে তার চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।
প্রথম পর্ব ছিলো: অধিকার ও দাবির সাথে নিজেদের হক আদায় করা। এ পর্বে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালু ছিলো।
দ্বিতীয় পর্ব: অনুরোধ আবেদন-নিবেদন ও আবদার করে নিজেদের হক আদায় করা। হিন্দুস্তান স্বাধীন হওয়ার পরও বহু বছর পর্যন্ত এ পর্বে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলতে থাকে।
তৃতীয় পর্ব: সবকিছু থেকে হাত ধুয়ে ফেলার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং এর উপর প্রশান্তি প্রকাশ করা। বরং খিলাফত, ইমারাত, নেতৃত্ব ও রাজনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা আজ পর্যন্ত এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে জীবন কাটিয়ে চলছি।
সারকথা
সারকথা হিসাবে কিছু বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি-
* তৎকালীন নেতৃত্বের কথা ও কাজে এ বিষয়ে একবারেই স্পষ্ট ছিলো যে, হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য তাদের কর্মপ্রয়াস, চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো দ্বারা তারা একটি দারুল হারবকে একটি দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায় উদ্দেশ্য ছিলো না।
* হিন্দুস্তান স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠি এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উলামায়ে কেরামের হাত থেকে বের হয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। যার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই বিষয়ক সকল আদান-প্রদান রাজনৈতিক নেতারাই সম্পন্ন করে।
* এই নেতারা হিন্দুস্তানকে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন করে ইসলামের পরিবর্তে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে গেছে।
* আর তাছাড়া রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটিশ শাসনের আইন-কানুন স্বাধীন হিন্দুস্তানে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজনও বোধ করেনি।
আরেকটি বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটন:
মুহতারাম পাঠকবর্গের মনোযোগকে আমি আরেকটি বাস্তবতার দিকে সম্প্রসারিত করতে চাই। আর তা হচ্ছে, ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্টের দিনকে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে স্মরণ করা হয়, যা সম্পূর্ণই ভুল ও ধোঁকা। এই দিন দুটিতে না পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, আর না ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই দিনে ভারত উপমহাদেশ মূলত টুকরা টুকরা হয়েছিলো। একটি টুকরাকে ভারত রাজ্য নাম দেওয়া হয়েছে এবং অপরটিকে পাকিস্তান রাজ্য নাম দেওয়া হয়েছে।
এক টুকরার পরিচয় ছিলো এই-
সরকারি সংবিধান: বাদশাহী।বাদশাহ: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জর্জ ষষ্ঠ।গভর্নর জেনারেল: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাউন্ট বেটন।
প্রধানমন্ত্রী: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জওহর লাল নেহেরু।আর অপর টুকরার পরিচয় ছিলো অনেকটা এরকম-
সরকারি সংবিধান: বাদশাহী।বাদশাহ: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জর্জ ষষ্ঠ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।গভর্নর জেনারেল: মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
এগুলো হচ্ছে ইতিহাসের সেসব বাস্তব চিত্র যা সাধারণ জনগণ ও সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে এ সত্যগুলোকে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এ ভারত উপমহাদেশে বহু রকমের পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু একটি বিষয় যার মাঝে কোনও পরিবর্তন আসেনি, তা হচ্ছে হিন্দুস্তান দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়নি। যার ফলে দুই টুকরার কোনও টুকরার শিরোনামই দারুল ইসলাম ছিলো না।
একই কারণে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করার কোনও বিষয় আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তই ছিলো না। ভারত বিভক্তের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হিজরত করা ওয়াজিব হওয়া কিংবা হারাম হওয়া বিষয়ক কোনও আলোচনাই আলোচ্য বিষয়ে স্থান পায়নি। উভয় অংশের কোটি কোটি মুসলমানের জন্য শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী? এর তাহকীক ও তালাশ কোথাও কোনো আলোচনার আলোচ্য বিষয় ছিলোই না এবং এর কোনো সুযোগও ছিলো না। কিছু মানুষকে মুহাজির নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে আনসার কারা ছিলেন? হিজরতের বিধি-বিধান ও মাসায়েলের প্রয়োগ না সীমানার এ পাড়ে ছিলো, আর না ওই পাড়ে ছিলো।
সব শেষ কথা হচ্ছে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ যাকে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা দিবস মনে করা হয়, সে সময়ে ভারত ও পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেছে ঠিক, কিন্তু হিন্দুস্তান দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হতে পারেনি। না এ অংশ, আর না সে অংশ।
হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে পাকিস্তান বিভক্ত ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত
(১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)
যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হিন্দুস্তানকে দুই টুকরা করা তথা বিভক্ত তো করেছে, কিন্তু তারা বহাল তবিয়তে উভয় অংশের উপর রাজত্ব করতে থাকে। আর যখন তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে, তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি ও দালালরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করবে, তখন তারা তাদের প্রতিনিধিদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইখতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। নবগঠিত দুটি রাজ্যে অবস্থাদির চিত্র অনেকটা এরকম ছিলো-
* আদালতগুলোতে সেসব আইন-কানুনেরই অনুসরণ চলছিলো যে আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দুস্তানকে পরিচালনা করে আসছিলো।* উভয় রাজ্যে মাশায়েখে ইসলাম ও উম্মতের রাহবারগণকে রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রভাবশালী পদগুলো থেকে অনেক দূরে রাখা হয়েছে।* উভয় অংশে গণতন্ত্র মজবুতভাবে তার নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।* উভয় অংশে ধর্মনিরপেক্ষতা আপন মূলনীতি ও আকীদা বিশ্বাসের উপর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।
* বিভক্তির আগে মুসলমানরা তাদের দীনের উপর যে পরিমাণ আমল করতে পারতো, নিজেদের গণ্ডির মাঝে যতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারতো, বিভক্তির পর কোনও রাজ্যেই সে পরিমাণও বাস্তবায়ন করা সম্ভব থাকেনি।* উভয় অংশে কোনও আইন-কানুনের কোনও একটি শাখাও পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হত না।* সীমানার উভয় প্রান্তে আইন প্রণয়ন পরিষদে কুরআন-হাদীস অথবা ফিকহে ইসলামীর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলাকে একটি অনর্থক ও হাস্যকর বিষয় মনে করা হত।* উভয় অংশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর প্রয়োগকৃত আইন-কানুন যে কেউ তৈরি করতে পারতো, হোক সে হিন্দু, কিংবা শিখ, অথবা বৌদ্ধ, কিংবা ইহুদী বা খ্রিস্টান।
* যেকোনো ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের বিচারপতি ও শাসক হতে পারে। তারা তাদের উপর যেকোনো প্রকারের আইন জারি করতে পারে। এ অংশেও, ওই অংশেও।* ইসলামী খিলাফত, ইসলামী ইমারত ও শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্র হাতে নেওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ অংশেও, ওই অংশেও।
উল্লিখিত শিরোনাম ও দফাগুলোর বিশ্লেষণ অনেক বিস্তৃত। আপনি বলতে পারেন, বিগত এক শতাব্দীকাল যাবৎ ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহগুলো এ শিরোনামগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, যা আমাদের বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষরা দেখেছেন, আর এখন আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখে চলেছি।
ভারতের মুসলমানরা আহলে কিতাব শাসকদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে, আর অমনি তাদের উপর মুশরিক শাসক এসে চেপে বসেছে। ভারত শাসন ব্যবস্থা শতভাগ গায়রুল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুসলমানদেরকে যখন যতটুকু দিতে চায়, তখন ততটুকু দিয়ে দেয়। কখনও পার্লামেন্টের কোনও চেয়ার, কখনও প্রশাসনের কোনও পদ, কখনও কোনও জলসার সভাপতিত্ব, আবার কখনও মাদরাসা মসজিদে কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠিয়ে দেওয়া, আর কখনও রাষ্ট্রীয় কোনও অবদানের জন্য শুভেচ্ছা-স্বাগতমের ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা দেওয়া ইত্যাদি।
অপর দিকে পাকিস্তানের শাসকরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, কিন্তু নিজেকে শিয়া রাফেযী পরিচয় দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। সবাই গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ; ইসলামী আইন বাস্তবায়নকে বৈধ মনে করে না। মানব রচিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে মূল তরিকা ও আসল সহীহ পদ্ধতি মনে করে।
গায়রে শরয়ী আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনাকে জরুরি মনে করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের উপর গায়রে শরয়ী শাসন এবং কুফরী নীতি চালিয়ে নেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তা করে। মুসলমানদের উপর কুফরী আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে যেখানে যেখানে বাধার সম্মুখীন হয়, সেখানে কিছু নিফাক আর কিছু মিথ্যা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়।
পাকিস্তান এভাবেই চলছিলো, আর এভাবেই বাইশ-তেইশ বছর কেটে গেছে। এরপর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের ক্ষমতাশীলদের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। পাকিস্তান দুই টুকরা হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশ অস্তিত্ব লাভ করে।
পাকিস্তান বিভক্তি এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান পর্যন্ত
(১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)
যাদের হাতে বাংলাদেশ অস্তিত্ব লাভ করেছে তারা নিফাকের মালা গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে সুস্পষ্ট ভাষায় কুফরের ঘোষণা দেয় এবং চারটি সর্ব স্বীকৃত কুফরী মূলনীতির উপর সংবিধানের ভিত্তি রাখার কথা ঘোষণা করে। মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ডের যে দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেছে, সে ধারণাকেই মূল থেকে মুছে দেওয়া হয় এবং আইনের যেখানে যেখানে ইসলাম ও মুসলমানের উল্লেখ আছে সেখান থেকে সে শব্দগুলো তুলে দিয়ে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশি অথবা এ জাতীয় কোনও শব্দ ব্যবহার করা হয়।
দেশের সংবিধান হুবহু সে সংবিধানই যা ব্রিটিশ শাসনামলে ছিলো এবং যা অখণ্ড পাকিস্তান থাকা কালে ছিলো। রাষ্ট্র যন্ত্রের কোনও পর্যায়ের কোনও পদের জন্য ইসলাম অথবা মুসলমান হওয়ার শর্ত নেই। আইন প্রণয়ন পরিষদ, সর্বস্তরের বিচারপতি, রাষ্ট্রপ্রধান মোটকথা প্রত্যেকটি পদে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনও প্রকার পার্থক্য রাখা হয়নি। এ অবস্থাই ব্রিটিশ ভারত, স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান ও আজকের বাংলাদেশে সকল পর্বে, সব সময়ে অব্যাহত থাকে।
ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু করে আজ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর পর্যন্তও যে বিষয়গুলোতে কোনও প্রকার পরিবর্তন আসেনি সেগুলো হচ্ছে এই-
* প্রত্যেক যুগেই এবং প্রত্যেক পর্বেই দেশের সংবিধান গায়রে ইসলামী ছিলো এবং এখন পর্যন্তও গায়রে ইসলামীই আছে।
* শাসন ও নেতৃত্ব মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। মুসলিম অমুসলিম সবারই এ অধিকার আছে যে, সে ক্ষমতার আসনে বসবে এবং সবার উপর শাসনের লাঠি ঘোরাবে। আইনগতভাবেই এটা সবার অধিকার।
* সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের কোনও প্রকার দখল নেই এবং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে কোনও প্রকার দাবি তোলারও অধিকার নেই। দাবি তোলার অধিকার আছে বলে যাকে উল্লেখ করা হয় তাও কুফরী সংবিধানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক পরে রাষ্ট্রীয় কিছু সুবিধার জন্য শরীয়াহ বেঞ্চের ভিত্তি রাখা হয়েছে। কিন্তু তার কোনও ফায়দা মুসলমানদের কপালে জোটেনি।
* আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ যেকোনও ধর্মের হতে পারে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে এবং সে আইন মুসলমানরা মানতে বাধ্য।
* ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধি-বিধানের খেলাফ অসংখ্য আইন ও সিদ্ধান্তাবলি রয়েছে। আর যে আইনগুলো শরীয়তের খেলাফ নয়, সেগুলোও কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হওয়ার কারণে আসেনি; বরং ঘটনাক্রমে তা হয়ে গেছে।
* এসকল গায়রে শরয়ী আইনের অনুসরণ করার উপর এবং এর বিপরীত না করার উপর অঙ্গীকার করা জরুরি।
* শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ফরয ওয়াজিবগুলোর তালীম, তাবলীগ এবং সেগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অনুমতি নেই। বরং ঈমানের সকল শাখার তালীম, তাবলীগ ও উদ্বুদ্ধ করণ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।
* যিনা, মদ্যপান, সুদ, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরও বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া। কাফের ও আইম্মাতুল কুফরের সাথে বন্ধুত্ব, জিহাদের প্রতিরোধ এবং মুজাহিদদেরকে সব ধরনের গাল-মন্দ করার বৈধতা দেয়া। খিলাফত ও ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধ করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে মানবতা বিরোধী কাজ বলে সাব্যস্ত করা, ইসলাম ও গায়রে ইসলামের ভিত্তিতে জিহাদ করাকে অবৈধ সাব্যস্ত করা এবং এ ধ্যান-ধারণাকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত করা। দারুল ইসলাম ও দারুল হারব শিরোনামে পৃথিবী ভাগ করাকে হঠকারিতা, মৌলবাদী চিন্তাধারা, পশ্চাদপদ মানসিকতা ও সন্ত্রাসবাদ হিসাবে চিহ্নিত করা।
শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত কাফেরদের সঙ্গ দেওয়া। ইলমে দীন শিক্ষাকে ওয়াজিব হিসাবে সাব্যস্ত না করা। মুসলমানদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করার জন্য বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করা। অমুসলিমদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস এবং তাদের কুফরের প্রচার, প্রসার ও শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান, সরকারিভাবে তার ব্যবস্থাপনা, তার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, সার্বিক সহযোগিতা করা এবং তাদের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। ইসলামের বিধি-বিধানের উপর আমল করার জন্য গায়রে ইসলামী সংবিধানের সাথে মিল রাখা জরুরি এবং ইসলামী বিধি-বিধানের উপর আমল করার জন্য গায়রে ইসলামী সংবিধানের দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া জরুরি হওয়াসহ এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে।
এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহিমাহুল্লাহ যে পরিস্থিতিতে এবং যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে এ ভূখণ্ড তথা ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, হুবহু সে পরিস্থিতি ও সে বিষয়গুলো এখনও বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে উপস্থিত রয়েছে।
বিভক্তির পর এ তিনটি দেশ নিজ নিজ অবস্থানে নিজ নিজ পদক্ষেপ ও শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে এ বার্তা দিতে থাকে যে, ইসলাম ও মুসলিম শিরোনামে এ দেশগুলোতে শাসন করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তারা এ বার্তা দিতে থাকে যে, আইন প্রণয়ন পরিষদের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কোনো মূলনীতিকে আইনের মর্যাদা দেওয়া, কুরআন-হাদীসের আলোকে চলমান কোনও আইনকে অকার্যকর করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ তিন দেশের আদালতগুলোতে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে কোনও আইনের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করাকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার সমার্থবোধক মনে করা হয়। বাস্তবতা এটাই।
পাকিস্তানের শরীয়া বেঞ্চ দেখে কেউ ধোঁকা খাবেন না
আমরা আগেও উল্লেখ করে এসেছি যে, পাকিস্তানে শরীয়া বেঞ্চ শিরোনামে যে বেঞ্চ রয়েছে, বছরের পর বছর পর্যন্ত এর কোনও অস্তিত্ব ছিলো না। আর যখন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তা আদালতি কার্যক্রমের শত ভাগের এক ভাগকেও আওতাভুক্ত করতে পারেনি। তাছাড়া কোনও দেশে আলাদাভাবে শরীয়া বেঞ্চের উপস্থিতিই এ কথা প্রমাণ করে যে, সে দেশের আইন-কানুন কুফরী ও গায়রে শরয়ী। এ ‘শক্তি ও সামর্থ্য’দিয়ে পাকিস্তানের এ শরীয়া বেঞ্চ দেশের আইনের খেলাফ কখনও কোনও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাতে পারেনি। সর্ব স্বীকৃত সুদের মাসআলা নিয়ে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আকাবির উলামায়ে কেরাম নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা অনর্থক প্রমাণিত হয়।
ইতিহাসের কিছু পৃষ্ঠা উল্টানোর পর
এ পর্যায়ে আমি দুটি আয়াতের দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ এই দুটি আয়াতই আমাদের জন্য সান্ত্বনা ও প্রশান্তির আধার।
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
“ওই জাতি তো অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কামাই করেছে তা তাদের জন্য, আর তোমরা যা করবে তা তোমাদের জন্য। তাদের আমলের বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।” -সূরা বাকারা ০২:১৩৪
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى *
“ সে (অর্থাৎ ফেরাউন মূসাকে লক্ষ্য করে) বললো, আচ্ছা বলতো, আগের লোকদের কী অবস্থা? মূসা বলল, তাদের বিষয়ে জ্ঞান আমার রবের কাছে কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না।” -সূরা তহা ২০:৫১-৫২
বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, খায়রুল কুরূনের পর সালাফে সালেহীনের যতগুলো তাবাকা ও স্তর রয়েছে তাঁরা সবাই অবশ্যই আমাদের পূর্বসূরি ও আমাদের অগ্রপথিক পথ প্রদর্শক, কিন্তু চার দলীলের বিপরীতে তাঁরা আমাদের জন্য হুজ্জত কিংবা দলীল নয়। তাঁদের খাস কোনও কর্মপদ্ধতি অথবা চিন্তা-চেতনার বিষয়ে সুনিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়াও আমাদের জিম্মাদারি নয় এবং শরয়ী দলীলের বিপরীতে তাঁদেরকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। শরয়ী যেকোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপদ্ধতির সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের সামনে কুরআন মাজীদ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেইশ বছরের নববী জীবন রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর শরীয়ত অনুশীলন ও প্রয়োগের শত বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
আমাদের দুর্বলতা
এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে এসেছে, যা না বলে চলে যাওয়া সমীচীন মনে হয় না। তা হচ্ছে, মক্কার মূর্তিপূজারি মুশরিকরা সাইয়েদিনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাদের মুক্তাদা বা অনুকরণীয় পূর্বসূরি মনে করতো। নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের বংশধর বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতো। ইহুদীরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ইহুদী মনে করতো, আর খ্রিস্টানরা তাঁকে খ্রিস্টান মনে করতো। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন-
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
“ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলিম, আর তিনি মুশরিকও ছিলেন না। নিঃসন্দেহে ইবরাহীমের সবচাইতে কাছের লোক একমাত্র তারাই যারা তাঁর অনুকরণ করছে, আর এ নবী এবং যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ এ মুমিনদের সঙ্গে রয়েছেন।”-সূরা আলে ইমরান ০৩:৬৭-৬৮
বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সর্বস্বীকৃতি ব্যক্তিবর্গকে নিজের পূর্বসূরি হিসাবে প্রকাশ করতে সবাই আগ্রহী থাকে, কিন্তু তাঁদের যথাযথ অনুসরণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরামও বার বার এ পরিস্থিতিরি মুখোমুখি হয়েছেন। কেউ আছে যারা নিজেদেরকে ওয়ালিউল্লাহি চিন্তাধারার ধারক-বাহক বলে দাবি করে, কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর সংস্কারমূলক অবদানগুলোকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহিমাহুল্লাহর নাম উচ্চারণ করে গর্ববোধ করে, তাঁর ফাতওয়া তাদের মনকে জয় করে, কিন্তু তাঁর ফাতওয়া গ্রহণ করে সে মোতাবাকে আমল করা থেকে মন পালিয়ে বেড়ায়।
সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুমুল্লাহর জিহাদী জযবার সাথে একমত বলে প্রকাশ পায়, কিন্তু জিহাদের কথা বললে নাক ছিটকাতে থাকে। মক্কী, গাঙ্গুহী, নানুতাবীর নাম উল্লেখ করলে মন-মস্তিষ্ক, দেহ-প্রাণে সতেজতা ফুটে উঠে, কিন্তু শত্রু নিধনের জন্য নিজের প্রাণ ও মাল কুরবান করাকে বৈধ মনে করে না। শায়খুল হিন্দের স্মরণে গর্বে বুক ফুলে যায়, কিন্তু খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ করাকে নাজায়েয মনে করে।
যাইহোক, এগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু দুর্বলতা। কিন্তু যে যাই বলুক, আমাদের করার মতো কাজ শুধু একটি। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত শরীয়ত, আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া আদর্শ। তাই ইতিহাসের এ সংক্ষিপ্ত দাস্তান উল্লেখ করার পর এবার সেসব জিম্মাদারি ও দায়িত্ব নিয়ে কথা বলবো, যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের উপর বর্তায়। আল্লাহ সঠিক কথা বলার তাওফীক দান করুন।
(ইনশাআল্লাহ চলবে)
আরও পড়ুনঃ ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই কেন ওয়াজিব? (৩য় পর্ব)