আত্মপরিচয়ের যুদ্ধ: বাংলার মুসলিম বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ
আত্মপরিচয়ের যুদ্ধ: বাংলার মুসলিম বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ
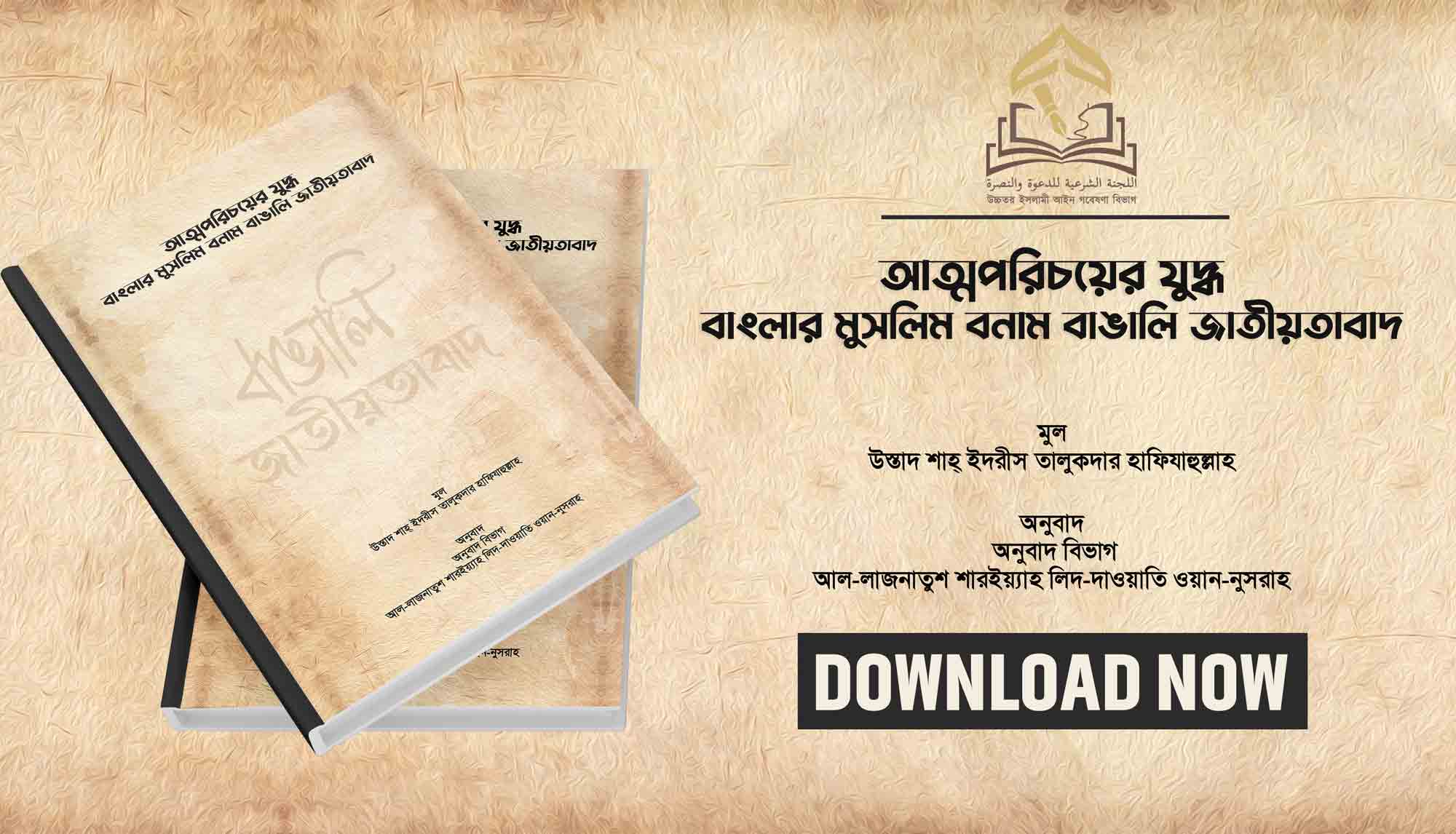
পিডিএফ ডাউনলোড করুন
ওয়ার্ড ডাউনলোড করুন
মূল
উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ
অনুবাদ
অনুবাদ বিভাগ
আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
সূচিপত্র
প্রথম স্তর: বাংলায় মুসলিম শাসনামল (১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল). 9
দ্বিতীয় স্তর: বাঙালি রেনেসাঁ (১৭৬৭ থেকে ১৯৪৭ সাল). 13
তৃতীয় স্তর: পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (১৯৫২-১৯৭৫). 18
চতুর্থ স্তর: শাহবাগ বনাম শাপলা (২০১৩ থেকে এখন পর্যন্ত). 21
ভূমিকা
সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ’র ‘আত্মপরিচয়ের যুদ্ধ: বাংলার মুসলিম বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় লেখক বাংলার মুসলিম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, কারণ ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া, পলাশীর যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের সাথে দুর্গাপূজার সম্পর্কের বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধারণা কাদের থেকে এসেছে, কীভাবে এটাকে বাংলার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে – সে বিষয়টিও স্পষ্টভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। পরিশেষে বাংলার মুসলিমদের আত্মপরিচয়ের এই সংকটে ইসলামের সমাধান কি – সেটিও আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের করণীয় সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা পাব ইনশাআল্লাহ।
এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে ‘জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা’র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন ‘শেনাখ্ত কী জঙ্গ: বাংগালি কওম পুরুস্তি বামুকাবেলাহ্ মুসলিম বাংগাল’ (شناخت كی جنگ: بنگالی قوم پرستی بمقابلہ مسلم بنگال) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির মূল বাংলা অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।
আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়দা ব্যাপক করুন! আমীন।
সম্পাদক
19 শাবান, ১৪৪৪ হিজরী
১২ই মার্চ, ২০২৩ ইংরেজি
আত্মপরিচয়ের যুদ্ধ: বাংলার মুসলিম বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ
উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ
আমাদের এই আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল; বাংলাদেশের অধিবাসীদের ‘বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ’ ও ‘বাংলার মুসলিম’ হিসেবে পরিচয় এর মধ্যকার বিবাদের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করা। চারটি ‘মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী’ ধাপ বিশ্লেষণ করে, এই পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক পরিচয়গুলোর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।
প্রথম যে স্তরের পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে তা হল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আগের যুগ। এসময় বাংলা মুসলিম শাসনাধীন ছিলো। রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্বশীল এবং নীতি নির্ধারক মহল এই অঞ্চলের গৌরবময় ইতিহাস, সমৃদ্ধি ও ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক বাহক ছিলেন।
দ্বিতীয় স্তরটি হল; ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। এসময় বহিরাগত প্রভাবের কারণে কলকাতার (পশ্চিম বাংলার) হিন্দু অভিজাতদের চেষ্টায় একটি ‘বাঙ্গালী হিন্দু’ পরিচয়ের সৃষ্টি হয় এবং তা বিস্তার লাভ করে। এই আন্দোলনটি ‘বাঙালি রেনেসাঁ’ নামে প্রসিদ্ধ। এই রেনেসাঁর উদ্ভাবক এবং প্রবক্তারা বৈদিক বর্ণনা, গল্প-কাহিনী এবং হিন্দুদের ঐতিহ্য থেকে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। সেই সাথে তারা পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলো।
তৃতীয় স্তরটি – ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরের যুগ। বিশেষ করে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যবর্তী সময়। এসময় একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়, যা সর্বশেষ পাকিস্তানে বেসামরিক যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলাফল বয়ে আনে। এই নতুন জন্ম নেয়া রাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়ি এমন একটি সংবিধান ও আইন নিয়ে আসে, যা কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উপর তৈরি করা হয়েছিলো।
চতুর্থ স্তরটি হল – ২০১৩ সালের শাহবাগ এবং শাপলা চত্বরের আন্দোলন। এসময় বাঙালি-মুসলিম পরিচয়ের দ্বন্দ্ব পুনরায় সামনে আসে। এই শেষ স্তরটি আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক এখনও চরম মাত্রায় বিপরীতমুখী। এই প্রেক্ষাপটে কিছু মানুষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ের সমর্থক। এদের মধ্যে আছে – ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, বামপন্থী এবং গ্লোবালিস্টরা। গ্লোবালিস্ট বলতে তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যারা বৈশ্বিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। চাই তারা আওয়ামী লীগের শাসনের সমর্থক হোক বা বিরোধী। আবার কিছু মানুষ (অর্থাৎ দীনদার মুসলিমরা) একটি ইসলামী পরিচয়ের উন্নতি চায়।
আমাদের আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো – এই চারটি স্তরকে গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলিমদের পরিচয়ের জটিল ও বহুমুখী সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা। ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ককে সূক্ষ্ম ও সর্বাঙ্গীণভাবে স্পষ্ট করা।
পারস্পরিক পরিচয়-যুদ্ধ
বাংলাদেশে ‘বাঙালি’ ও ‘মুসলিম’ এই দুটি পরিচয় প্রায় পরস্পরবিরোধী ও বিপরীত। একটিকে অপরটির সাংঘর্ষিক মনে করা হয়। বাঙালি পরিচয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাংলা অঞ্চলে (বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গে) বসবাসকারী জাতিগুলোর সভ্যতা, ভাষা ও বংশ নির্ভর স্বীকৃতি। বর্তমানে এই ‘বাঙালি’ পরিচয়ের অঞ্চলটি অনেকগুলো শিরকী আকীদা-বিশ্বাস, রুসুম-রেওয়াজ ও পাশ্চাত্য রেনেসাঁর সৃষ্টি করা দার্শনিক ধারণা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত।
অন্যদিকে ‘বাংলার মুসলিম’ পরিচয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। এই পরিচয় এই অঞ্চলের ‘দীর্ঘ ও একক ইসলামী ইতিহাস’ এবং ‘মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে’র মতো চেতনাগুলো থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এটি এমন একটি চেতনা যা সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের মাঝেই বিদ্যমান।
‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। আর ‘বাঙালিত্ব’ বলতে – বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সভ্যতার খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, রুচি ও স্বভাব ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝায়। এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করা খুবই জরুরি।
বাংলাদেশে ‘বাঙালি’ ও ‘বাংলার মুসলিম’ এর বিরোধপূর্ণ পরিচয়ের চিত্র ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এবং ১৯৪৭ এর ভারত ভাগের সময় দেখা গিয়েছে। এই ভাগের ফলস্বরূপ পাকিস্তানের জন্ম হয়।
বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান ‘উর্দু’ ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ফলে বাঙ্গালীরা বিক্ষোভ করে। অতঃপর ১৯৬০ এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের সময় পাকিস্তান আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সর্বশেষ সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছে।
বাংলাদেশে এখনও ‘বাঙালি’ এবং ‘বাংলার মুসলিম’ এর পরিচয়ের বিষয়টা আলাপ-আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের কারণ হয়ে আছে। ৫০ বছর ধরে দখলদার ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য হল – ইসলামী পরিচয়ের উপর সেক্যুলার পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়া। এটা শুধু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ইচ্ছা নয়, বরং তাদের বিরোধী দল বিএনপিও এটাই চায়।
ঐতিহাসিক চারটি স্তর
প্রথম স্তর: বাংলায় মুসলিম শাসনামল (১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল)
পূর্ব বাংলার ইসলামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও গৌরবময়। বর্তমানে পূর্ব বাংলার বাসিন্দাদের ৯০ শতাংশ মুসলিম। পশ্চিম বাংলার (ভারতের অংশের) শুধু ৩০ শতাংশ মুসলিম। পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের এত বড় অংশ ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়া – এটা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।
বাংলার এই ‘এলাকা’টি পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় অনেক দূরবর্তী এবং নদী মোহনার নিকটবর্তী (অর্থাৎ বাংলার এই ব-দ্বীপ অঞ্চল – সামুদ্রিক ঝড় এবং অন্যান্য আসমানি বিপদাপদে অধিক আক্রান্ত হয়)। এই এলাকার বাসিন্দারা ব-দ্বীপ অঞ্চলের পশ্চিম অংশের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করেছে। মূলত ইসলামের গৌরবময় ও উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি পূর্ব বাংলাতেই হয়েছে, যা এখন ‘বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক রিচার্ড এম.ইটন লেখেন:
“মুসলিম শাসকগণ উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা শাসন করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলোর মধ্যে শুধু বাংলার (এটা এমন এক এলাকা, যার আয়তন ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের আয়তনের সমষ্টির সমান প্রায়) আদি বাসিন্দাদের অধিকাংশই অকল্পনীয়ভাবে শাসক শ্রেণির ধর্ম গ্রহণ করে নেয়।” (The Rise of Islam and the Bengal Frontier, Richard M. Eaton)
প্রথম দিকে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজীর বিজয়ী সৈন্য দলের সাথে গৌড়, পুণ্ড্র এবং লখনৌতিতে আগমন করে। এটাকেই পরবর্তীতে মুসলিম শাসকগণ ‘বাংলা’ এবং ব্রিটিশ সরকার ‘বেঙ্গল’ নাম দেয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে এর পূর্বে আরব, পারস্য, আফগানিস্তান এবং আনাতোলিয়া (আন্তাকিয়া বা অ্যান্টিওক) বাসিদের কোনও সম্পর্ক ছিলো না।
প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং কুমিল্লার ময়নামতিতে আব্বাসী শাসনামলের মুদ্রা পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মুদ্রার গায়ে ৭৮৮ ঈসায়ী সালের তারিখ দেয়া ছিলো। সম্ভবত তা হারুনুর রশিদের জামানার। আর ময়নামতিতে পাওয়া মুদ্রা আব্বাসী খলীফা মুনতাসির বিল্লাহর খিলাফত কালের।
এখানে এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহিমাহুল্লাহ ৭১৪ ঈসায়ীতে সিন্ধু বিজয় করেন। অর্থাৎ ইখতিয়ার খলজী তাঁর সৈন্য নিয়ে আসার প্রায় চারশো বছর আগে। ইখতিয়ার খলজীর আগমনে বাংলার তৎকালীন সেন শাসনের সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেন তার সিংহাসন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। সে মোটামুটি দূরে গিয়ে ঢাকার নিকটবর্তী এবং উপকূলীয় এলাকা বিক্রমপুরকে তার কেন্দ্র করে নেয়। তার মৃত্যুর পরে সেন রাজ বংশের অন্য রাজারাও বাংলার এই ছোট্ট অংশের উপর আরও অর্ধশত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে। অতঃপর মুসলিম সেনাপতি মুগিসউদ্দীন তুগরল পূর্ব বাংলাও বিজয় করে নেন। এই বিজয়ের পরে এই এলাকায় ইসলাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। পাশাপাশি মুসলিমদের রাজনৈতিক শক্তি – হিন্দুস্তানে বাংলার নিকটবর্তী ও আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ও বিস্তার লাভ করার সুযোগ হয়ে যায়।
যা হোক, এই মুসলিম শাসকদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম বাংলার তীরবর্তী সমস্ত এলাকাকে এক শাসন ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন তিনি হলেন – সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ্ সোনারগাঁও দখল করে নেন। ফলে পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দুস্তানে একটি নতুন ও ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি অস্তিত্বে আসে।
ইলিয়াস শাহ্ প্রথম শাসক যিনি ‘বাংলার সুলতান’ উপাধি গ্রহণ করেন। এখানেই ঐ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় যা আকবর ‘বাংলা প্রদেশ’ এবং ব্রিটিশরা ‘বেঙ্গল’ নামে অভিহিত করেছে। ইলিয়াস শাহ্ পূর্ব বাংলার তৎকালীন রাজধানীর উপর হামলা করার আগে, সোনারগাঁওয়ের শাসক ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ এর ইন্তেকালের অপেক্ষা করেন। মোবারক শাহের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে সোনারগাঁওয়ে আক্রমণ করেন। রাজধানী বিজয় হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব বাংলার বিজয় সম্পন্ন হয়ে যায়।
প্রসিদ্ধ মরোক্কান পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ এর শাসনামলে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ফখরুদ্দিনের শাসনাধীন এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সচ্ছল অবস্থা দেখে খুব প্রভাবিত হন। তিনি এটা বিশেষভাবে অনুভব করেন যে, বাংলার টেক্সটাইল (অর্থাৎ পোশাক শিল্প) গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অবস্থানে আছে। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কম ছিলো এবং মানুষজন সাধারণত ভালো অবস্থায় ছিলো। প্রসিদ্ধ কবি শাহ্ জালালের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো।
ইলিয়াস শাহ্ এর হাতে বাংলার সালতানাত প্রতিষ্ঠা এবং প্রায় দুই শতাব্দীর মুক্ত ও স্বাধীন সরকারের আমলে মুসলিম শাসকগণ অনেকগুলো বহিঃরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বাংলায় স্বাধীন ইসলামী সরকার সাড়ে পাঁচশত বছরের দীর্ঘ সময়, এমনকি ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর ময়দানে পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এই পুরো সময়ে বাংলা ইলিয়াস শাহ্ এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ ছিলো।
বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও উন্নতিও ‘বাংলার ইসলামী সালতানাতের’ কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বাংলায় ইসলামী শাসনের পূর্বে ব্রাহ্মণ শাসন ব্যবস্থায় সাহিত্য ও বক্তৃতার ময়দানে কোন স্থানীয় বা দেশীয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগ ছিলো না। সেন রাজ বংশের শাসকরা সংস্কৃত ভাষার শুধু পৃষ্ঠপোষকতাই করতো না, বরং শিক্ষা বা সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার মতো অন্যান্য দেশীয় ভাষা ব্যবহারের উপরও তাদের পক্ষ থেকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিলো। সেন শাসকরা এবং প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যেকোন ‘দেশীয় ভাষা’কে সাহিত্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সকল চেষ্টাকে এই বলে নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করতো যে; হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ এবং পুরাণগুলোকে বাংলা ভাষায় লেখা বা পড়া- অবমাননা ও অবজ্ঞার কাজ।
সংস্কৃত ভাষার একটি প্রসিদ্ধ কবিতাতে এই সতর্কবাণী আছে যে, ‘কেউ যদি বাংলা ভাষায় রামায়ণ বা মহাভারত শোনে, সে পরের জন্মে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করবে’। মুসলিমদের বিজয় স্থানীয়দেরকে জ্ঞানের অঙ্গনে ব্রাহ্মণদের এই আধিপত্য থেকে মুক্তি দেয়। বাংলায় রাজনৈতিক ইসলামের আবির্ভাব এবং মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এমনকি বাঙালি হিন্দুরাও খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করে। বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য প্রথম রচনা হল – জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ এর আমলে কবি কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের অনুবাদ। হিন্দু শিক্ষাবিদ এবং বাংলা লোকসাহিত্য গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের সদস্য দীনেশ চন্দ্র সেন ১৮৯৬ সালে লিখেন:
“এত বড় দাপটশালী ও হাঁক ডাকওয়ালা রাজ দরবারে বাংলা ভাষা কিভাবে প্রবেশ করলো? ব্রাহ্মণরা এই ভাষাকে কি পরিমাণ তাচ্ছিল্যতার দৃষ্টিতে দেখতো তা আগেই জানা হয়েছে। এই অবস্থায় তারা বাংলা ভাষার উপর এমনিতেই এত দয়ালু কিভাবে হল?! আমার মতে, বাংলা ভাষার সুদিনের মূল কারণ হল, মুসলিমদের হাতে বাংলা বিজয় হওয়া।” [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস) – দীনেশ চন্দ্র সেন]
দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ উভয় জায়গাতেই, বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য বাংলার মুসলিম শাসকগণ যে ভূমিকা রেখেছিলেন তার যথাযথ মর্যাদা খুব কমই পাওয়া যায়। এই উদাসীনতা ও অজ্ঞতার একটি কারণ এই হতে পারে যে, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছি। আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসকদেরকে পরাজিত করেছিলো। ব্রিটিশরা মুসলিম শাসকদের প্রতি ঘৃণার কারণে, ব্রিটিশ উপনিবেশের একশ নব্বই বছরের পুরো সময়কালে, হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসকে মুছে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালিয়েছিলো।
এটাও একটা কারণ ছিলো যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মুসলিম সংখ্যালঘুদের চাইতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদেরকে খুশি ও সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলো। ক্ষমতাশালী হিন্দু জেনারেল এবং ব্যবসায়ীদের একটি দল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এই হিন্দুরা এবং তাদের উত্তরসূরিরা বাংলার ইসলামী যুগের গৌরবময় ইতিহাস মুছে দেয়ার ব্যাপারে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে।
১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর, পাকিস্তান সরকারও পূর্ব পাকিস্তানের লোকদেরকে এবং তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে একই দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে। তারা বাংলার গৌরবময় ইতিহাস, সমৃদ্ধি ও ইসলামের ঐতিহ্যকে বুঝা তো দূরের কথা, এর জন্য কখনও চেষ্টাও করেনি। ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশিরা স্থানীয় শক্তি এবং আমাদের নিকৃষ্ট প্রতিবেশী ভারতের তীব্র সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখেও কোন না কোনও ভাবে আমাদের মূল শিকড় এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অন্বেষণের সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছি।
দ্বিতীয় স্তর: বাঙালি রেনেসাঁ (১৭৬৭ থেকে ১৯৪৭ সাল)
‘বাঙালি রেনেসাঁ’ যাকে ‘নবজাগরণ’ও বলা হয়, সেটি ঊনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে হিন্দুস্তানের বাংলা অঞ্চলে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের যুগের নাম। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৫ থেকে ১৮৩৩) থেকে শুরু হয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ থেকে ১৯৪১) সময়ে এসে এটা শেষ হয়। এরপরেও এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, যারা এই পুনর্জাগরণের বিভিন্ন দিক সামলেছেন।
বাঙালি এই রেনেসাঁর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, এ অঞ্চলে পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়া। বাংলায় পশ্চিমা ধাঁচে স্কুল এবং কলেজ খোলাতে অনেক বাঙালি পশ্চিমা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনে জড়িয়ে পড়ে। যা তাদেরকে তাদের জাতিভেদ প্রথা এবং মূর্তি পূজার অযৌক্তিক হিন্দুত্ববাদী বিশ্বাসকে পুনঃনিরীক্ষণে বাধ্য করে। এই রেনেসাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ও আবেগ। অনেক লেখক এবং বুদ্ধিজীবী নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু করেন। তাদের অনেকেই এই ভাষার প্রতিষ্ঠা, উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করেছেন।
বাঙালি রেনেসাঁকে ঠিকভাবে বুঝার জন্য আবশ্যক হল, বাঙালি হিন্দুদের মনের ভাব বুঝা। তারা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখে – এটা পরিষ্কার বুঝতে হবে।
অনেক বাঙালি হিন্দু পলাশীর ময়দানে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে সীমাহীন আনন্দিত হয়েছিল। মূলত নবাবের পরাজয় ছিলো তাদের দীর্ঘ দিনের আশা পূরণ; যার জন্য তারা ইংরেজদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সমর্থন করে আসছিলো। বিশেষ করে ঐ হিন্দুরা, যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারকে নিজেদের অর্থনীতি ও সম্পদের স্বার্থে উপকারী মনে করেছে। এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ বিশেষভাবে দুইজন এবং তাদের বংশধরদের নিয়ে আলোচনা করবো। তাদের মধ্যে একজন ছিল কৃষ্ণ নগরের রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র, আর দ্বিতীয় জন ছিল কলকাতার নব কৃষ্ণ।
দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, যা হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পালন করা হয়। এই উৎসব দশ দিন ধরে উদযাপন করা হয়। বর্তমানে দুর্গা পূজাকে বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুরা পরিপূর্ণ আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং বিশ্বাসের সাথে দুর্গা পূজা পালন করে। এই উৎসবের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস হলো; এটি মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় এবং এর উদযাপন।
কিন্তু বাস্তবতা হল, হিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষের সাথে এই উৎসবের গভীর এবং মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। অনেক হিন্দু ইংরেজ ও সিরাজউদ্দৌলার মধ্যকার যুদ্ধকে দেও-অসুর যুদ্ধ (অর্থাৎ দেবতা ও শয়তানের মাঝে যুদ্ধ) শব্দে উল্লেখ করে।
একজন হিন্দু বুদ্ধিজীবী তার প্রবন্ধ ‘কলকাতার দুর্গা উৎসব’ এ লিখেছেন যে, দুর্গা পূজা মূলত পলাশীর বিজয়ের আনন্দ উদযাপন। আর এটা জানা কথা যে, সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার উৎসব ১৭৫৭ সালে নদীয়া এবং কলকাতায় বিজয় উদযাপন হিসেবে পালন করা হয়। কৃষ্ণ চন্দ্র নদীয়ায় এই পূজার সূচনা করে আর নব কৃষ্ণ কলকাতায় শুরু করে। কলকাতায় নব কৃষ্ণের ঘরে হওয়া দুর্গাপূজা উদযাপনে লর্ড ক্লাইভও অংশগ্রহণ করেছিলো। মুর্শিদাবাদে নবাবের ভাণ্ডার লুট করা এবং ক্লাইভের অনুগ্রহ ও সহযোগিতায় সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে এই দুই খান্দান।
সুতরাং বর্তমানে দুর্গাপূজার যে উৎসব পালন করা হয় তা মূলত হিন্দুদের বিজয় উৎসব। হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য রবার্ট ক্লাইভ এটি চালু করিয়েছিলো। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে কলকাতার প্রসিদ্ধ পত্রিকা ‘দ্য স্টেটসম্যান’ এ ‘যখন দুর্গা রথে আরোহণ করে (When Durga rode a Mlechcha)’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তপতী বসু লিখেন:
“পলাশীর যুদ্ধে বিজয় হয়ে গিয়েছিলো। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হয়েছে। কিন্তু হিন্দুদেরকে আয়ত্ত করা তখনও বাকি ছিলো। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়কে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের বিজয় হিসেবে পেশ করাটাই যথেষ্ট ছিলো না। তাই রবার্ট ক্লাইভ তার প্রতারক ও ধোঁকাবাজ সাথি রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায় এবং নব কৃষ্ণ দেব এর সাহায্য ও পরামর্শে দুর্গাপূজার হিন্দু উৎসব আয়োজন করে বিজয় উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এতে একটি সমস্যা ছিলো। ক্লাইভ বছরের ভুল সময়ে এই বিজয় অর্জন করেছে। অর্থাৎ ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে। তাই তারা পণ্ডিতদের সাথে পরামর্শ করতে বসে। নব কৃষ্ণদেব লৌকিকতা করে ‘অকাল বোধন’ (অর্থাৎ অসময়ে জেগে উঠার) উৎসব আয়োজন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কলকাতায় এটা এখনও পালিত হয়।
ক্লাইভ হিন্দুদের এই কূট-কৌশল খুব ভালোভাবে কাজে লাগায়। পূজার এই উৎসবকে সফল করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ লুকিয়ে ফেলেছে এবং সীমাহীন সফলতা পায়।”
পলাশীর যুদ্ধের আগে দুর্গাপূজা শরৎ কালে পালিত হতো না। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে এই বিজয়কে হিন্দুদের বিজয়ের আকৃতি দেয়ার জন্য এবং হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য ক্লাইভ একটি উৎসবের আয়োজন করার চিন্তা করে। এই উৎসবটি দুর্গাপূজার উৎসবের মতো করে পালন করা হয়। ধীরে ধীরে মুসলিমদের উপর বিজয়ের এই উৎসব পুরা দুনিয়ায় দুর্গাপূজা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।
কলকাতার হিন্দু মাতব্বররা, যারা নিজেদের ঘরে ইংরেজদেরকে আমন্ত্রণ করতো, তারা ভালোভাবেই জানতো যে, ‘সাহেব লোকেরা’ শুধু মাটির তৈরি পুতুল দেখে খুশি হবে না। তাই সাহেবদের জন্য রক্ত মাংসে গড়া পুতুলের ব্যবস্থা করে। তারা ব্রিটিশ অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ গানের আয়োজনে এবং পতিতা সংগ্রহে পানির মতো টাকা খরচ করে। এই পতিতাদের কিছু লাক্ষ্মৌ থেকে এনেছে, কিছু বার্মা থেকে এবং কিছু স্বয়ং ইংল্যান্ড থেকেই নিয়ে এসেছে। এই মহিলাদেরকে ‘বাই’ বা ‘বাই জি’ (রাণী, নর্তকী ইত্যাদি) বলা হত। সুতরাং একই সময়ে উঠানের এক প্রান্তে হিন্দুরা তাদের মূর্তির জন্য মঞ্চ তৈরি করতো আর অন্য প্রান্তে আনন্দ বিনোদনের জন্য নাচ গানের আয়োজন করতো। যেনা, অশ্লীলতা, সঙ্গীত এবং নাচ-গান সব সময়ের জন্য দুর্গাপূজার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।
এটাই ছিলো সেই ক্ষেত্র ও সুযোগ যার মাধ্যমে বাঙালি রেনেসাঁ অস্তিত্বে আসে। এই পরিবেশ থেকেই ‘বাঙালি’র বিশেষ পরিচয়ের সৃষ্টি হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাঙালির এই চিন্তাগত আকৃতিতে হিন্দুত্ববাদী শিরকী সংস্কৃতি এবং পশ্চিমা চিন্তা-দর্শন – উভয়ের মিশ্রণ ছিলো।
যদিও হিন্দুস্তানে ইংরেজ সরকারের মূল কেন্দ্র ছিলো কলকাতায়, তা সত্ত্বেও তারা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদেরকে পর্যায়ক্রমে ও ধীরে-ধীরে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
১৭৯৩ সালে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন’ এর অধীনে অনেক মুসলিম জমিদার থেকে তাদের জমি ছিনিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর এই আইনের সাহায্যে এবং ইংরেজদের আশীর্বাদে অনেক হিন্দু কেরানি ও গোমস্তা স্বয়ং জমিদার হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। ইংরেজরা বাঙালি কৃষকদের (যারা অধিকাংশই মুসলিম ছিলো) জন্যও ফসলের উপর একটি অতি কঠিন নিয়ম জারি করে। ইংরেজ সরকারের হিন্দু-মুসলিম বিষয়ে দ্বিমুখী আচরণ এবং মুসলিম অভিজাতদেরকে নিঃস্ব করে দেয়ার নীতির ফলে মুসলিমরা পিছিয়ে পরে। এ সুযোগে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি অভিজাতদের একটি শ্রেণি সৃষ্টি হয়। এই ধনী ও সম্পদশালী লোকেরাই বেসামরিক সেবা, আদালত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নিয়েছিলো।
যদিও হিন্দু ও মুসলিমরা একই সমাজে এবং একই সরকার ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করত, তবুও তাদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবন একরকম ছিলো না। বাঙালি মুসলিম এলাকার মুক্ত ও স্বাধীন মুসলিম শাসকদের পরাজয়ের কারণে মুসলিমরা ইংরেজ এবং তাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী ছিলো। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার ঘোরবিরোধী ছিলো। এর বিপরীতে হিন্দুরা ইংরেজদেরকে তাদের নাজাত দাতা ও তাদের মতো হিন্দুই মনে করতো।
শিক্ষা, সাহিত্য এবং অর্থনীতির ময়দানে হিন্দু নেতারা কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দু সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। এটা এমন এক ধারাবাহিক কার্যক্রম ছিলো, মুসলিমরা যাতে অসন্তুষ্ট হলেও বাঁধা দেয়া বা বন্ধ করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।
ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে ইসলাম এবং হিন্দুস্তানের মুসলিমদেরকে অবজ্ঞা করা, তাদের সম্মানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা একটা সাধারণ বিষয় ছিলো। হিন্দুস্তানের মুঘল সালতানাতের ভেঙ্গে পড়া কাঠামোর উপর ব্রিটিশ উপনিবেশিক দখলদারিত্বকে বৈধতা দেয়ার জন্য ব্রিটিশ লেখক, বুদ্ধিজীবী, আমলা এবং মিশনারিরা মুসলিমদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাকেই সহজ ও সঠিক সমাধান বলে মনে করেছিলো। তাই সংঘবদ্ধভাবে মুসলিমদেরকে ‘অত্যন্ত খারাপ’ ও ‘জরাজীর্ণ’ বলে চিত্রায়িত করতে শুরু করে।
শীঘ্রই হিন্দুস্তানের উদীয়মান লেখকরা ব্রিটিশদেরই জ্ঞান ও সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ শুরু করে। এই লেখকরা হিন্দুস্তানের ইসলাম ও মুসলিমদের (কৃতিত্ব)কে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের বিকৃতি ঘটিয়েছিলো। এসকল লেখকদের চিন্তা-ভাবনা ইউরোপিয়ান প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারার কাছাকাছি ছিলো। এরা এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান এবং বিস্তৃত উপনিবেশবাদকে সমর্থন করতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে অনেক হিন্দু লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের হাত ছিলো। এরা মুসলিমদের কৃতিত্বকে খর্ব করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলো।
তৃতীয় স্তর: পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (১৯৫২-১৯৭৫)
১৯৫০ এবং ৬০ এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক, রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজাতদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিলো। এই অসন্তোষ ন্যায্য ছিলো। কারণ সামরিক ও রাজনৈতিক অভিজাতদের সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি নিয়মিত এবং পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতো এবং সেখানকার জনগণকে অপমান ও অপদস্থ করতো। অথচ যে লোকদের সাথে এই আচরণ করা হত তাদের অধিকাংশই ছিলো মুসলিম, যারা সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহের সাথে পাকিস্তান সৃষ্টিকে সমর্থন করেছিলো। অবস্থা এমন ছিলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের এই অভিজাতরা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমদের দীন ও ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তুলতেও দ্বিধা করেনি। অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য, অবমাননা ও অবজ্ঞামূলক আচরণ – পরবর্তীতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ, ঘৃণা, তিক্ততা ও অসন্তুষ্টির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতারা জনগণের এই অনুভূতির পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। তারা একটি ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন’ শুরু করেছিলো, যার অনেক চিন্তা ও ধারণা ‘বাঙালি রেনেসাঁ’ থেকে ধার করা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রলেপ লাগিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি’র পথ সুগম করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো।
যদিও এই দলগুলোর চিন্তার উৎস ছিলো বাঙালি রেনেসাঁ, তবে তারা সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদেরও প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলো। এরা পশ্চিমা উদারতাবাদ এবং মার্কসবাদ থেকে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দার্শনিক যুক্তি গ্রহণ করতো এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (যিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন) কবিতা, সংগীত, নাটক এবং প্রবন্ধকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির জন্য নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করতো। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করার জন্য তারা ‘বাঙ্গালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িকতা’র কথা প্রচার করতো। এই গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপগুলি নতুন ছিলো না, বরং তারা ১৯৩০ এর দশকের শেষ থেকে সক্রিয় ছিলো।
১৯৬০-এর দশকে রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র নেতাদের আরেকটি দল একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবি করতে এবং তা সমর্থন করতে শুরু করে। এই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আধুনিকতাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। নাস্তিকতাবাদ ও উদারতাবাদের সংমিশ্রণ তাদেরকে এমন একটি মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়, যার ফলে ১৯৭২ সালের সংবিধানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে মূলনীতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।
এটাও স্পষ্ট যে, বুদ্ধিজীবীদের এই দলটি পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়নের পটভূমিতে মার্কসবাদী বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলো। তারা লেনিনের ‘রাশিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাস’ (Economic History of Russia) এর প্রশংসা ও গুণগান করতো। কেউ কেউ লিওন ট্রটস্কির ‘স্থায়ী বিপ্লবের ধারণা’ (Idea of Permanent Revolution by Leon Trotsky) এর বাংলা অনুবাদও করেছে।
মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভিতরগত সার্কেলের মানসিকতা বোঝার জন্য এই আলোচনা ও গবেষণার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এই দলগুলোই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ বিতর্ককে প্রচার, প্রসার ও রূপ দেয়ার প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধান রচনা ও প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই শ্রেণির সদস্যদের গভীর ও মৌলিক সম্পর্ক ছিলো। (তাদের তৈরি করা) ঐ আইন ও বাংলাদেশ সংবিধানই ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতির স্থান দিয়েছে।
এখানে এটা জানা জরুরি যে, পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মার্কসবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিপ্লবের পক্ষে ছিলো না। পাকিস্তানের ইসলামী পরিচয়ের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে কোনও বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছিলো না। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা ছিলো মুসলিম। তারা যেমনিভাবে নিজেদের মুসলিম মনে করতো, একইভাবে তারা এটাও চেয়েছিলো যে, বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মতো তাদেরকেও সমান মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার দেয়া হোক।
এটা বোধগম্য যে, শাসকশ্রেণির প্রতি তাদের ক্ষোভের অনুভূতি ছিলো। কিন্তু তাদের এই ক্ষোভ এবং আক্রমণাত্মক অনুভূতিকে সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতারা এবং বামপন্থী সমর্থকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলো। আওয়ামী লীগ সরকার, ছাত্র সংগঠনগুলো এবং বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে গিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবমাননা করতে ত্রুটি করেনি। অথচ এর সাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের গভীর আবেগের সম্পর্ক ছিলো। তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরোধিতা আর মুসলিম পরিচয় ও ইসলামের বিরোধিতাকে সমার্থক বানিয়ে নিয়েছিলো।
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের খসড়া তৈরি করা হয়। দুঃখের বিষয় হল, বাঙালি সভ্যতা বা জাতীয়তাবাদের নামে আওয়ামী লীগ সরকার এই অঞ্চলের মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র – এগুলোর সমষ্টিকে (মুজিবের নেসবতে) ‘মুজিববাদ’ বলা হয়। এই ‘মুজিববাদ’ ছিলো দেশের নতুন আদর্শিক প্লাটফরম এবং ‘জয় বাংলা’র স্লোগান ছিলো বাংলাদেশের নতুন দেশপ্রেমের স্লোগান। তৎকালীন সরকার জনগণের রাজনৈতিক অনুভূতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুস্পষ্ট প্রতিশোধমূলক মনোভাব নিয়ে রাস্তাঘাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের মতো অর্থহীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলো।
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আওয়ামী অনুষ্ঠান শুরু করা একটি পুরানো ঐতিহ্য ছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের নতুন সরকার ১৯৭২ সালে এই ঐতিহ্যেরও অবসান ঘটায়। পাকিস্তান আমলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিলো শুক্রবার, কিন্তু পরে তাও পরিবর্তন করে রবিবার করা হয়। আরেকটি চরম পদক্ষেপ হল, ইসলামপন্থী সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করা।
১৯৭৫ সালে সেনাবাহিনী মুজিবকে উৎখাত করে এবং মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। কিন্তু এরপর যে সরকারগুলো এসেছে তারাও তাদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে অটল থেকেছে। তারা মানব রচিত আইনে শাসন করতে থাকে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে বল প্রয়োগ করে দমন করে। হ্যাঁ, মুজিব যুগের খোলামেলা ও স্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে এসে তারা অনেকাংশে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ও পূর্ববর্তী শাসকদের মতো ইসলামিক পরিচয়ের কিছু বাহ্যিক ও বিশেষ দিক গ্রহণ করতে শুরু করে।
আজ বাংলাদেশে চারদিক থেকে ইসলামের উপর আগ্রাসন চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিমরা এখনও আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহর ভালোবাসা বুকে জড়িয়ে রেখেছে।
১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর সময়কালে, মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন পশ্চিমা রাজনৈতিক ধারণা ও মতাদর্শের আলোকে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’কে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতো। মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই বুদ্ধিজীবীরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পরিচিত করতে থাকে। কিন্তু তাদের প্রচারণা ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের এসব বর্ণনা মুসলিম জনগণের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে ছিলো।
চতুর্থ স্তর: শাহবাগ বনাম শাপলা (২০১৩ থেকে এখন পর্যন্ত)
চতুর্থ পর্যায় শুরু হয় ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলন থেকে। আন্দোলনে ১৯৭১ এর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানানো হয়। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরাসহ অনেক নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বলেছেন যে, এই অভিযোগ এবং এর উপর ভিত্তি করে বিচার করা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিলো; ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলো না।
শাহবাগ আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর সব নেতাকে হত্যার দাবি নিয়ে এসেছিলো। এই আন্দোলন বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলো। এর জন্য তারা নিয়মিত রাজনৈতিক প্রচারণাও চালিয়েছে। মৌলিকভাবে এই আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে ছিলো বামপন্থী ছাত্রদলগুলো, বুদ্ধিজীবী, আওয়ামী লীগ এবং বিশেষ করে ভারত। আন্দোলনের উত্থানকালে যারা যোগ দিয়েছিলো তাদের বিনামূল্যে খাবার এবং মিডিয়া কভারেজ নিশ্চিত করা হয়েছিলো। এর ফলে অনেক মানুষ তাদের সমাবেশে যোগ দিয়েছিলো। যা হোক, প্রাথমিকভাবে দেশের অনেকে এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলো।
লক্ষণীয় বিষয় হল; শাহবাগ আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় সংগঠক এবং সাহসী প্ররোচনাকারীদের মধ্যে সে সকল ব্লগারও ছিলো যারা প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন রাযিয়াল্লাহু আনহাদের অপমান করেছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে শাহবাগ আন্দোলনের প্রথম দিকেই মুজাহিদরা শাতেমে রাসূলদের থেকে রাজীব নামক একজন জঘন্য ব্যক্তিকে হত্যা করতে সক্ষম হন। এই হত্যাকাণ্ডের পরে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজীবের বাসায় গিয়ে তাকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ‘প্রথম শহীদ’ ঘোষণা করে। এর কিছুদিন পর যখন রাজীব এবং শাহবাগ আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের অশ্লীল (পর্নোগ্রাফিক) ও ইসলাম বিরোধী লেখাগুলো জনসাধারণের সামনে আসে তখন আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং লোকেরা তাদের বয়কট করতে শুরু করে।
তখনই কওমি মাদরাসার আলেমদের নেতৃত্বে হেফাযতে ইসলাম নামের সংগঠন শাতেমিনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আবারও গোটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। শাহবাগ আন্দোলন একঘরে হয়ে যায়, আর জনসাধারণের দৃষ্টি হেফাযতে ইসলামের দিকে ফিরে যায়।
সময়ের সাথে সাথে হেফাযতে ইসলামের আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। অতঃপর ২০১৩ সালের ৫ই মে ‘হেফাযতে ইসলাম আন্দোলন’ একটি লং মার্চ ঘোষণা করে। এটি ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে শাপলা চত্বরে শেষ হওয়ার কথা ছিলো। সরকার হেফাযতে ইসলামের বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালালে অনেক লোক মারা যায়। এরপর প্রবল সরকারি চাপের কারণে এই আন্দোলন দমে যায়। অন্যদিকে শাহবাগ আন্দোলন ধীরে ধীরে আপনা-আপনি শেষ হয়ে যায়।
কিন্তু দেশ শাপলা চত্বর এবং শাহবাগের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। সাধারণ জনগণের অনুভূতিকে অনুধাবন করে আওয়ামী লীগ সরকার ধীরে ধীরে শাহবাগ আন্দোলন এবং এর আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে দূরে সরতে শুরু করে।
যদিও হেফাযতে ইসলাম আন্দোলন এই গোস্তাখ ব্লগারদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে উপমহাদেশের আল-কায়েদার মুজাহিদরা এই অবাধ্য ব্লগারদের অনেককে শাস্তি দিতে সফল হয়েছে। আল-কায়েদার কর্মকাণ্ড এইসব উদ্ধতদেরকে নীরব করাতে এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ক্রমবর্ধমান জোয়ারকে থামাতে অত্যন্ত সফল হয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আবারও তীব্র গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং কোন ইসলামী আন্দোলন পর্যাপ্তভাবে এর গতি রোধ করতে সক্ষম হয়নি।
আজ ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ এবং ‘বাংলার মুসলিম’ পরিচয় এর দ্বন্দ্ব দেশকে বিভক্তকারী সবচেয়ে বড় এবং কেন্দ্রীয় আদর্শিক দ্বন্দ্ব।
সার কথা:
ইসলাম সব ধরনের সংস্কৃতিকে তার অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্যতা রাখে। তবে এই শর্তে যে, ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক শিরোনামগুলোকে বিলুপ্ত করে দিতে হবে। ইসলামের এই স্বভাব ও নীতির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বৈচিত্র্য ও গ্রহণযোগ্যতার অবস্থা সৃষ্টি হয়।
সমগ্র পৃথিবীতে বসবাসকারী মুসলিমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাদের খাবার ভিন্ন। পোশাক, অভ্যাস, বর্ণ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এইসব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তারা ইসলামের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত। ইসলাম তার অনুসারীদের উপর নির্দিষ্ট কোনও ভাষা বা রুসম-রেওয়াজ চাপিয়ে দেয় না। আর কোন এক জাতিকে অন্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠও মনে করে না। যদিও আরবী ভাষার একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। কেননা আরবী ভাষা শুধু ওহীর ভাষাই নয়, বরং তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও ভাষা। এই ভাষাতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নববী শিক্ষাগুলো প্রথম যুগের মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছেন।
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এবং আরও আলেমগণ এই ব্যাপারে লিখেছেন যে, কোন আরব ব্যক্তির অনারব ব্যক্তির উপর ফযীলত বা প্রাধান্য নেই এবং কোন আরব ব্যক্তির উপর অনারব ব্যক্তিরও ফযীলত বা প্রাধান্য নেই। কিন্তু মুসলিমদের জন্য আরব ও আরবী ভাষার প্রতি ভালোবাসা রাখা স্বভাবজাত বিষয় এবং ঈমানের অংশও (আর এটার কারণ তাই, যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি)। এই হিসেবে একটি মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়ে গড়ে উঠার সুযোগ থাকে।
তবে এই সাধারণ গ্রহণ যোগ্যতার জন্যও একটি শর্ত আছে। আর তা হল; ‘ইসলাম ও উম্মতে মুসলিমাহ’ – এই দুইটি বিষয় মুসলিমদের পরিচয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হতে হবে। যে সকল শিরোনাম এই দুটি বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এর মধ্যে সামাজিক ঐসব রুসম-রেওয়াজও অন্তর্ভুক্ত যা ইসলামী আদর্শের বিপরীত। যেমন, কুসংস্কার, বৈষম্য, আকীদাগত ভিন্নতা, প্রথা প্রচলন এবং ঐসব উৎসব যা ইসলামী আদর্শের বিপরীত।
উপমহাদেশের বাসিন্দাদের নিকট ইসলাম এটা দাবি করেনি যে, তাদেরকে আবশ্যকীয় ভাবে আরবদের খাবারে অভ্যস্ত হতে হবে! আর উত্তর আফ্রিকানদের থেকেও এটা চায়নি যে, তাদেরকে আফগানীদের মতো পোশাক পরিধান করতে হবে! মরক্কোর মুসলিমদের উপরও এটা চাপিয়ে দেয়নি যে, তাদেরকে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর মুসলিমদের রুসম-রেওয়াজকে গ্রহণ করতে হবে!
যদি কোন মুসলিমের উপর এধরনের কোন জোর-জবরদস্তি করা হয় এবং আল্লাহ তাআলা যে প্রশস্ততা দিয়েছেন তা মুসলিমদের জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয় তবে তা এই উম্মতকে কেবল দুর্বলই করবে। কেননা আসাবিয়্যাত (জাতীয়তা), কোন বিশেষ দলীয় পরিচয়, নিজ জাতি, ভূমি এবং ভাষার প্রতি ভালোবাসা – এই অনুভূতি আমাদের সবার মাঝেই লুকায়িত আছে। আর যখন এটা জাগ্রত হবে তখন কেউই এর প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবে না। তাই যদি কারও ভূমি, জাতি বা রুসম-রেওয়াজের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করা হয়, তবে এটা অবশ্যই তিক্ততা ও ঝগড়ার কারণ হবে।
সামষ্টিক ভাবে ইসলাম বনি আদমের মধ্যে তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও একতার অনুভূতিকে উন্নত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের দাবি পূরণ করা হবে ততক্ষণ জাতিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পছন্দ গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। ইসলাম সমাজের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈচিত্র্য এবং গ্রহণযোগ্যতার অনুমতি দেয়, যতক্ষণ দীনের মৌলিক কোন উসূলের ক্ষেত্রে আপোষ না হয়। তাই ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন তাহযীব ও সংস্কৃতির লোকদেরকে এক আকীদার পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করে।
সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বা এধরনের অন্য কোন ব্যাপারে কথা বলা বা মত দেয়ার ক্ষেত্রে এই মূলনীতিকে স্মরণ রাখা আবশ্যক। কেননা এই নীতি থেকে সরে যাওয়া, চাই তা উদাসীনতার কারণে হোক বা চরমপন্থার কারণে হোক, এর ফলে মুসলমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়, মতপার্থক্য তৈরি হয়, বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয়। এভাবেই অভিযান ও আগ্রাসন অনিবার্য হয়ে ওঠে।
আরও পড়ুনঃ ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই কেন ওয়াজিব? (৩য় পর্ব)




